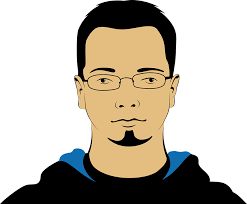

ইলিশের প্রজনন ও জীবনচক্র মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকির মুখে পড়েছে ইলিশ সম্পদ। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে উৎপাদনে। গত ৫ বছরে ধারাবাহিকভাবে ইলিশ উৎপাদন কমছে। আর উৎপাদন কমায় মাছটির দামও এখন স্বল্পআয়ের মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু ইলিশের উৎপাদন কমছে কেন?
মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মূলত: দুটি প্রধান কারণে ইলিশের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
একটি হলো: প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা। আরেকটি মানবসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে অভিবাসন রুটে প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূল আবহাওয়া, নদীর নাব্যতা হ্রাস ও দূষণ। আর মানবসৃষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে অবৈধ ট্রলিং, জাটকা ও মা ইলিশ ধরা এবং অবৈধ জালের ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও মাঠ পর্যায়ের তথ্যের আলোকে ইলিশ উৎপাদন হ্রাসের এই কারণগুলো খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা (বিএফআরআই)।
ইলিশের উৎপাদন কমার বিষয়টি স্বীকার করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারও। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে সম্প্রতি সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, গত ৫ বছরে ইলিশ আহরণ কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত ইলিশ আহরণ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, চলতি বছরের জুনের মাঝামাঝি সময়ে সারা দেশের ইলিশের জাটকা ইলিশ আহরণের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল বাজারে ইলিশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই ও আগস্ট মাসে ইলিশ আহরণ ২০২৪ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৩৩.২০ শতাংশ এবং ৪৭.৩১ শতাংশ কম হয়েছে। এই দুই মাসে মোট আহরণ হয়েছে ৩৫ হাজার ৯৯৩ দশমিক ৫০ মেট্রিক টন, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২২ হাজার ৯৪১ দশমিক ৭৮ মেট্রিক টন কম। যা শতাংশের হিসেবে ৩৮ দশমিক ৯৩।
বিএফআরআইর গবেষণা বলছে, ২০২৪ সালের নিষেধাজ্ঞার ফলে ৫২.৫ শতাংশ মা ইলিশ নিরাপদে ডিম ছেড়েছিল। এর ফলে ৪৪.২৫ হাজার কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে যুক্ত হয়েছে। এই ডিম থেকে উৎপন্ন রেণু বা পোনা (জাটকা) ভবিষ্যতে পরিপক্ব ইলিশে পরিণত হবে। তবে মা ইলিশ যে পরিমাণ ডিম ছেড়েছিল, যদি সে পরিমাণ পরিপক্ব ইলিশ পাওয়া যেত তাহলে ইলিশের উৎপাদন কমার কথা নয়। এর আগে বিএফআরআই-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ইলিশের ডিম পাড়ার হার ১১ শতাংশ বেড়েছে। সাধারণত ডিম যে পরিমাণে বাড়ে, ইলিশও তার কাছাকাছি পরিমাণে বাড়ে। কিন্তু ঐ একই সময়ে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ; অর্থাৎ ডিম পাড়ার হারের চেয়ে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ অর্ধেক। অর্থাৎ, ইলিশের উৎপাদন কমছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ইলিশ একটি পরিযায়ী মাছ, যা প্রজননের জন্য সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করে এবং ডিম ছাড়ার পর জাটকা বড় হয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। এই অভিবাসন চক্র সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মুক্ত ও বাধাহীন নদীপথ অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে মেঘনা, তেঁতুলিয়া, দৌলত খান ও চাঁদপুর অঞ্চলের নদীপথে অসংখ্য ডুবোচর সৃষ্টি হয়েছে। এসব চর মা ইলিশের স্বাভাবিক অভিবাসন রুটকে ব্যাহত করছে। চাঁদপুরের চর হাইচর, চরভৈরবী ও ইব্রাহিমপুর, ভোলার জাহাজ মারা ও হামতিয়াচর, পটুয়াখালীর দাসনারচর ও চরকলমাখালি এবং লক্ষ্মীপুর, ভোলা অঞ্চলের চরফ্যাশন ও চরআনন্দ প্রসাদ এলাকায় ডুবোচরের আধিক্য ইলিশের চলাচল ব্যাহত করছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে ইলিশ সম্পদ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে। নদীর নাব্য হ্রাস, পানির প্রবাহ পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষ করে প্রথম অভয়াশ্রম এলাকায় শীতকালে পানির মান দ্রুত নষ্ট হয়। অক্সিজেন (ডিও) কমে যায় এবং পানিতে অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা মাছের জন্য বিষাক্ত। এর ফলে ইলিশসহ অন্যান্য মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয় এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে শিল্প বর্জ্য, কৃষি রাসায়নিক এবং নগরবর্জ্য নদীতে মিশে পানির মান আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এই দূষণ ধীরে ধীরে মেঘনার নিম্ন প্রবাহে ছড়িয়ে পড়ছে, যা ইলিশের অভিবাসন রুট ও প্রজননক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করছে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট চাপও ইলিশ আহরণে বড় প্রভাব ফেলছে।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আমিরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে গতকাল ইত্তেফাককে জানান, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে ইলিশের প্রজনন ও জীবনচক্র মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। তিনি বলেন, ইলিশের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে অভিবাসন রুট সংরক্ষণ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ ট্রলিং বন্ধ করা এবং অবৈধ জালের ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।
https://shorturl.fm/DP8g5